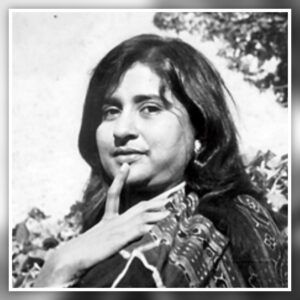১৯৭০ সালে নান্দীকার তার সভ্যদের দশটি প্রশ্ন করে। সকলেই লিখিত উত্তর দেয়। নান্দীকারের দশম বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক-পুস্তিকা(নান্দীকার ১৯৬০-১৯৭০)-র এই সংখ্যায় সেই সব উত্তর ছাপা হয়। বাংলা নাট্যমঞ্চের চিরকালীন নাট্য ব্যক্তিত্বের তালিকার অন্যতম নাম কেয়া চক্রবর্তী। কেয়া এই প্রশ্নগুলির জবাবে কি বলেছিলেন সেটা আমরা একবার ফিরে দেখে নিতে পারি। আলোচনায় : দীপেন্দু চৌধুরী

নান্দীকারের প্রশ্নের জবাবে
নাম, বাড়ির ঠিকানা, বয়স?
২০-এ রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬
জন্মঃ ৫ অগস্ট, ১৯৪২
কী করেন?
অধ্যাপনা।
কতদিন থিয়েটারে যুক্ত আছেন এবং কীভাবে?
মোটামুটি ভাবে ১৯৬১ সাল থেকে। অনিয়মিত ও অপেশাদারী ভাবে, এর আগেও স্কুল-কলেজে নাটক করেছি।
নান্দীকারে কবে এলেন? কেন? কী ভাবে এসেছেন?
১৯৬১ সালে প্রথম আসি। আমি থিয়েটার করতে চাইছিলাম। অন্যান্য দল সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। নান্দীকারে আমার পরিচিত লোকেরা কয়েকজন ছিলেন। তাই এসেছিলাম। কিন্তু ভেবে এসেছিলাম এমন নয়। ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য কিছুদিন পরে চলে যাই। পড়াশুনোর ক্ষতি, শরীর খারাপ, বাড়ির বকুনি, এইসব কারণে। পরে ১৯৬৬ সালে আবার আসি।
বর্তমান সময়ের কয়েকজন প্রথম সারির নাট্যব্যক্তিত্ব যতটা না পেশাদার তার থেকে অনেক বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সেটা পৃথক আর একটা বিষয়। ‘রক্তকরবী’-র প্রতিশ্রুতি বিশ্ব নাট্যদিবসের অঙ্গিকার। ১৯৬২সালে ইন্টারন্যাশন্যাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট (ITI) ২৭ মার্চ দিনটিকে বিশ্ব নাট্যদিবস হিসেবে ঘোষণা করে। যারা নাটক দেখেন, তাঁদের কাছে নাট্যশিল্পের মূল্যবোধ এবং গুরুত্ব পৌঁছে দেওয়াটাই নাট্যকর্মীদের কাজ।
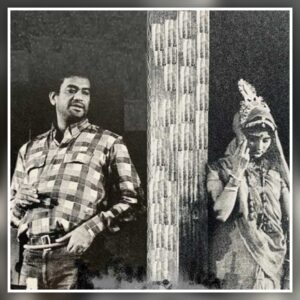
বাংলা নাটকের অন্যতম অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তীর কথা আমরা তুলে ধরলাম। তিনি নাটকে কেন এসেছিলেন সেটা নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীর পূরণ করা ফর্ম থেকে উল্লেখ করলাম। কেয়া চক্রবর্তীকে একটি সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়েছিল, নাটকতো আপনাকে কিছুই দেয়না, যেমন টাকা, পয়সা। তবু কেন নাটকেই আছেন? সব ছেড়ে দিয়েই নাটক করছেন?
কেয়া চক্রবর্তীর উত্তর, ‘আর্থিক অর্থে নাটক আমায় কিছু দেয় না। কিন্তু অন্য অর্থে এত বেশি দেয় যে এ নিয়ে দুঃখ করাটা বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। …আমার যেটুকু শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে সেটুকু ব্যবহার করার ক্ষেত্র করে দিচ্ছে থিয়েটার। আমার দল, পরিচালক এবং অন্যান্য কমরেডরা, এই তো যথেষ্ট। যদি কোনদিন আসে সৎ শিল্প থেকে সৎ উপার্জন করার, তবে আমার মতো সুখী লোক আর খুঁজে পাবেন না।’
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শম্ভু মিত্র, ভি শান্তারাম, উৎপল দত্ত, গিরিশ কারনাড, ভীষ্ম সাহানি, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মনোজ মিত্র, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্যের মতো নাট্যব্যক্তিত্ব ভারতীয় নাট্যমঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছে। দু’ই যুগের সমন্বয়ে বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নাট্যমঞ্চ হয়ে উঠেছে ধ্রুপদী শিল্প। কিন্তু হঠাত কোথায় একটা সীমাবদ্ধতা বাংলা নাটককে ভাবতে বলছে। কেন?
আমরা একুশ শতকের নাট্য-সংস্কৃতির পূর্ণবেলায় বসে রুদ্ধসঙ্গীতের বা রুদ্ধজনের ব্যক্তিত্ব খুঁজছি। পলাশ আগুনের ওমে বসে একুশে আইন সম্ভবত অনেকেই জানেন না। বিশেষত যারা বর্তমান প্রজন্মের অ্যান্ড্রয়েড যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন। অপরাধ তাঁদের নয়, দায়িত্ব আমারা নিতে পারিনি। তাই বাংলা নাটক নিয়ে বর্তমান সত্য উত্তর সময়ে কিছুটা আদিখ্যেতা হয়ত আছে। বলতে চাইছি, নাটক নিয়ে আনুষ্ঠানিকতা এবং আয়োজনের প্রচারমুখী চটক বা ঢক্কা-নিনাদ অনেক বেশি আছে। নাটকের বিষয়বস্তুর অভাবে। কিছু ভালো নাটক হচ্ছে, অস্বীকার করা যাবে না। তবু অনেক অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন নাটকের বিষয়ে বলতে গেলে আমার মনে পড়ছে নাট্যব্যক্তিত্ব শাওলী মিত্রের কথা। সংবাদমাধ্যমে কাজ করার সুবাদে অনেকের সংস্পর্শে আসার আমার সুযোগ হয়েছে। এই স্তম্ভে ২০১৬ সালে ‘পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা’-র জন্য নেওয়া শাওলী মিত্রের সাক্ষাৎকার থেকে টুকরো একটা অংশ উল্লেখ করছি। আমার প্রশ্ন ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে সামনে রেখেই কি ‘নাথবতী অনাথবৎ’ করতে হয়েছিল? শাওলীদির উত্তর, ‘না ঠিক তা নয়। প্রাথমিক ভাবে দ্রোপদী আমার কাছে একজন অতুলনীয় সহনশীল মানুষ হিসেবেই ধরা দিয়েছিল। মানুষ হিসেবেই তার প্রতি যে অন্যায় অবমাননা ঘটে চলেছে বছরের পর বছর আমার কাছে তা প্রতিবাদযোগ্য মনে হয়েছিল। সেই মনে করেই নাটকটি আমার কলম দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।’
এর পরেও শাওলীদি যেটা বলেছিলেন, দৈনিক কাগজে প্রকাশ হওয়া একটা খবর। মফঃস্বলের একটা মেয়ে কলেজে পড়তে আসত কলকাতা শহরে। ক’য়েকটা ছেলে প্রায় প্রতিদিন ওই মেয়েটিকে উত্যক্ত করত। না কোনও প্রতিবাদ ছিল না। মেয়েটি পড়াশোনায় ভালো। সম্ভবত সুশ্রী। তাই স্থানীয় কিছু ছেলে, যারা স্থানীয় রাজনৈতিক দাদার চেলা। রোজই তাঁকে স্টেশনে যাওয়ার পথে বিরক্ত করে। মেয়েটি পাত্তা দেয় না। এতে ছেলেগুলোর জেদ চাপে। তাদের মধ্যে বাজি হয়। রেল স্টেশনে একদিন একটি ছেলে অপেক্ষারত বহু লোকের সামনে ওই মেয়েটির মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে দেয়। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপরে এই মেয়েটিকে নিয়ে আর কোনও খবর দেখা যায়নি। শাওলীদি প্রশ্ন তুলেছিলেন, পরবর্তীতে তার পরিণতি নিয়ে ক’জন পাঠকেরই বা উৎসাহ থাকবে? ভারতীয় নাট্যপরিবারের অত্যন্ত সফল একজন নাট্যব্যক্তিত্ব শাওলী মিত্র। তিনি বলতে চেয়েছিলেন নাটকের দায়বদ্ধতার কথা।
পঞ্চরস, টুসু গান, গম্ভীরা, ছৌনৃত্যের উঠোন জুড়ে ধর্ম বা আদিরসের উপাদান থাকলেও সামাজিক দায়বদ্ধতাও থাকে। ওই ধারাকে অনুসরণ করেই আগামীর প্রতিশ্রুত উত্তরণ হয়েছিল গণণাট্যের মঞ্চে। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতু গড়ে দেওয়া সোভিয়েত রাশিয়ার লেবেদেভের পথেই। ধ্রুপদী নাট্য ব্যক্তিত্ব গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেভ। ১৭৮৭ সালে লেবেদেভ এসেছিলেন অবিভক্ত ভারতের কলকাতা শহরে। গণনাট্য থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, নিবেদিতা দাস। ওই সময়ে তাঁদের ত্যাগের কোনও সীমা পরিসীমা ছিল না। বিশেষ করে নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে। তৃপ্তি মিত্র ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে নাটক করেছেন। এই উদাহারণ খুব বেশি নেই।

বিশ্বায়ন উত্তর ভারতে বা বাংলায় তথা সারা বিশ্বে সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে। বর্তমানে সেই ত্যাগ বা আদর্শ আর দেখা যায়না। বর্তমান সময়ের কয়েকজন প্রথম সারির নাট্যব্যক্তিত্ব যতটা না পেশাদার তার থেকে অনেক বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সেটা পৃথক আর একটা বিষয়। ‘রক্তকরবী’-র প্রতিশ্রুতি বিশ্ব নাট্যদিবসের অঙ্গিকার। ১৯৬২সালে ইন্টারন্যাশন্যাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট (ITI) ২৭ মার্চ দিনটিকে বিশ্ব নাট্যদিবস হিসেবে ঘোষণা করে। যারা নাটক দেখেন, তাঁদের কাছে নাট্যশিল্পের মূল্যবোধ এবং গুরুত্ব পৌঁছে দেওয়াটাই নাট্যকর্মীদের কাজ। এবং সরকার, রাজনীতিবিদ, প্রতিষ্ঠানের দরজায় কড়া নাড়তে হবে। তাঁদের জন্য যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছে ন্যায়ের জন্য। মহাজনের অত্যচারের গল্প সৃজন করতে হবে। এক মুঠো আলোর জন্য। নাট্যমঞ্চের দায়িত্ব হচ্ছে সামাজিক দায়বদ্ধতার গল্প শোনানো।
ছবি : সংগৃহীত